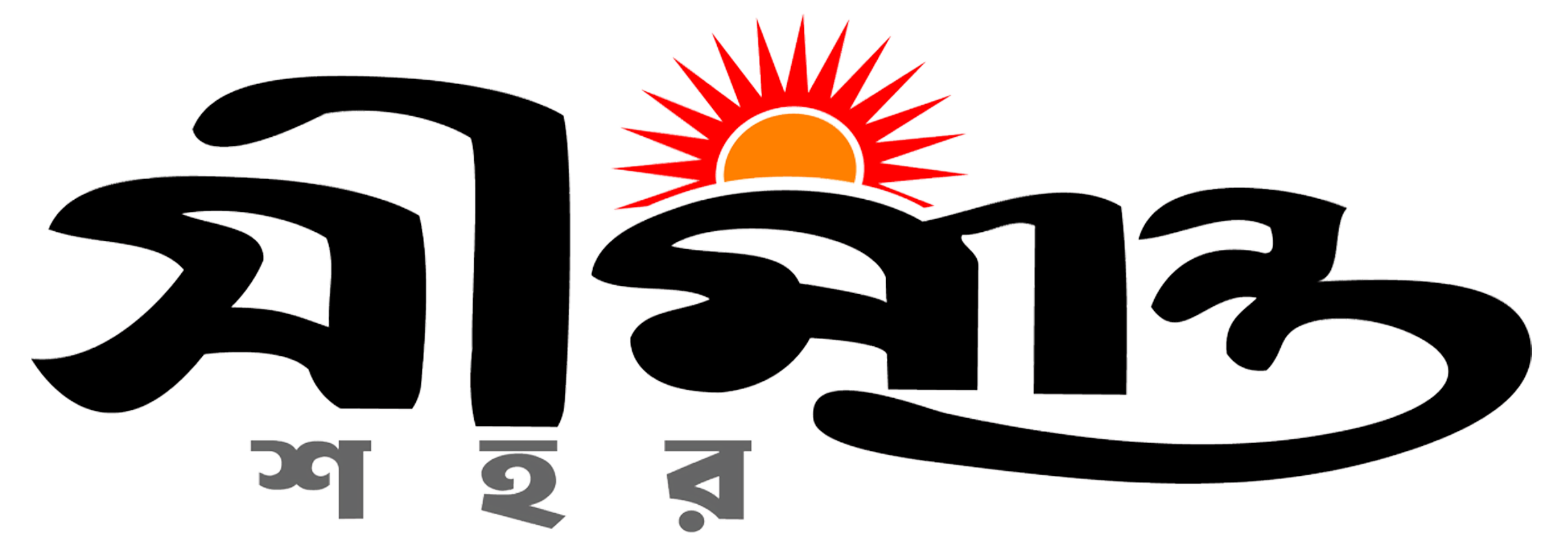
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসী শিক্ষার্থীদের অবদান কেন উপেক্ষিত?
 সুমাইয়া জাফরিন চৌধুরী, মালয়েশিয়া
সুমাইয়া জাফরিন চৌধুরী, মালয়েশিয়া
২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত হয়ে উঠেছিল। দেশজুড়ে যখন লাখো মানুষ ফ্যাসিজম, স্বৈরতন্ত্র, দমন-পীড়ন এবং দুর্ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে, তখন সেই ঢেউ শুধু সীমান্তের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল বিশ্বের নানা প্রান্তে—মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সৌদি আরব, কাতার, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে।
তারা সে সময় শুধু নৈতিক সংহতি প্রকাশ করেননি বরং নিজেদের স্বস্তি, নিরাপত্তা ও রুটিন জীবন বিসর্জন দিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন প্রতিবাদে। ক্লাস, অ্যাসাইনমেন্ট, চাকরি—সবকিছু একপাশে রেখে তারা রাতভর জেগে থেকেছেন। চোখ রেখেছেন দেশের খবরের দিকে, কোনো বন্ধুর ভাইয়ের খোঁজ মিলছে কি না, কোনো ভিডিও ফাঁস হচ্ছে কি না, কিংবা কোনো আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশের কথা আসছে কিনা—এই সব কিছুর জন্য সারা রাত স্ক্রিনে চোখ আটকে থেকেছে অসংখ্য তরুণ-তরুণী।
রান্না বন্ধ, নিয়মিত খাওয়া বন্ধ—সাধারণ ভাত-ডিম বা শুধু ভাত খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা না ঘুমিয়ে কেটেছে অনেকের রাত। দেশের মধ্যে থাকা পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন প্রবাসীদের অসহায়ত্ব যেন কয়েকগুণ বেড়ে যায়।
এই সময়ে তারা শুধু মানসিকভাবে নয়, বাস্তবভাবেও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেকেই অর্থ পাঠিয়েছেন—কারও জন্য খাবার কিনতে, কারও জন্য পানি পাঠাতে। কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে, কেউ দূতাবাস বা শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করেছেন, ব্যানার বানিয়েছেন, প্ল্যাকার্ড হাতে দেশের জন্য দাঁড়িয়েছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা চালিয়েছেন সচেতনতা বৃদ্ধির ক্যাম্পেইন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন, ভিডিও বানিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে। এমনকি কিছু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও মিডিয়া বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছে এই ডিজিটাল সক্রিয়তার চাপে।
তবুও, আন্দোলন-পরবর্তীতে যখন ইতিহাস লেখা হচ্ছে, সংহতির গল্প বলা হচ্ছে, তখন এই প্রবাসী অংশগ্রহণকারীরা প্রায় অদৃশ্য। তাদের অবদানকে আলাদা করে তেমনভাবে কোথাও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আন্দোলনের মূল্যায়ন এখনো মূলত মাঠে সরাসরি উপস্থিতির ভিত্তিতে হয়, যার ফলে প্রবাসীদের অনেকেরই ত্যাগ ‘দ্বিতীয় সারির’ বিবেচিত হয়। দেশের গণমাধ্যমগুলোও সেসময় প্রবাসীদের আন্দোলনকে বিশেষ কাভারেজ দেয়নি, ফলে সাধারণ জনগণের কাছে এই ভূমিকা আজও অজানা রয়ে গেছে।
আরেকটি কারণ, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব কাঠামোতে প্রবাসীদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। যদিও অনেক প্রবাসী শিক্ষার্থী নেতৃত্ব দেন নিজেদের জায়গা থেকে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সংগঠন বা মুখপাত্র হিসেবে তারা ছিলেন না। তার ওপর, প্রবাসীরা অধিকাংশই কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র না হয়ে নিরপেক্ষ অবস্থানে ছিলেন। এই নিরপেক্ষতা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর কাছে ‘অচেনা’ বা ‘অগ্রহণযোগ্য’ হয়ে দাঁড়ায়, যা ইতিহাসে তাদের অনুল্লিখিত রাখার একটি কারণ হয়ে ওঠে।
তবে এই অবজ্ঞা শুধু ইতিহাসের প্রতি অবিচার নয় বরং ভবিষ্যতের জন্য একটি বিপজ্জনক বার্তা। কারণ, পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা লাখ লাখ বাংলাদেশি যদি ভাবতে থাকেন—তাদের সংগ্রাম কখনোই স্বীকৃতি পায় না, তাহলে তারা ভবিষ্যতে এই ধরনের সংকটে অংশ নিতে নিরুৎসাহী হয়ে পড়বেন। ফলে শুধু আন্দোলন দুর্বল হবে না, দেশের সঙ্গে তাদের আত্মিক বন্ধনও দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যাবে।
২০২৪ সালের অভ্যুত্থান একটি জাতীয় নয় বরং একটি বৈশ্বিক নৈতিক জাগরণ ছিল। দেশের ভেতরে এবং বাইরে থাকা মানুষ একসঙ্গে সোচ্চার হয়েছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সেই জাগরণে প্রবাসী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল নিঃসন্দেহে সাহসিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাদের চোখে জল ছিল, হাতে ছিল মোবাইল আর বুকের ভেতর ছিল জ্বলন্ত দেশপ্রেম। তারা চুপচাপ বসে থাকেনি, বরং চিৎকার করে বলেছিল—‘আমরা আছি, আমরা দেখছি, আমরা দাঁড়িয়েছি।’
এই বাস্তবতায় সময় এসেছে তাদের অবদানকে ইতিহাসের মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার। স্বীকৃতি দেওয়া মানে শুধু ন্যায় প্রতিষ্ঠা নয়, বরং একটি প্রজন্মের আত্মত্যাগকে সম্মান জানানো।
প্রবাসীদের কণ্ঠকে প্রান্তিক করে রাখলে ইতিহাস যেমন অপূর্ণ থেকে যাবে, তেমনি গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে পড়বে।
Cox's Bazar Office: Main Road, Kolatli, Cox's Bazar, Bangladesh.
Ukhia Office: Main Road, Ukhia, Cox's Bazar, Bangladesh.
Email: shimantoshohor@gmail.com
© 2025 Shimantoshohor.com. All rights reserved.